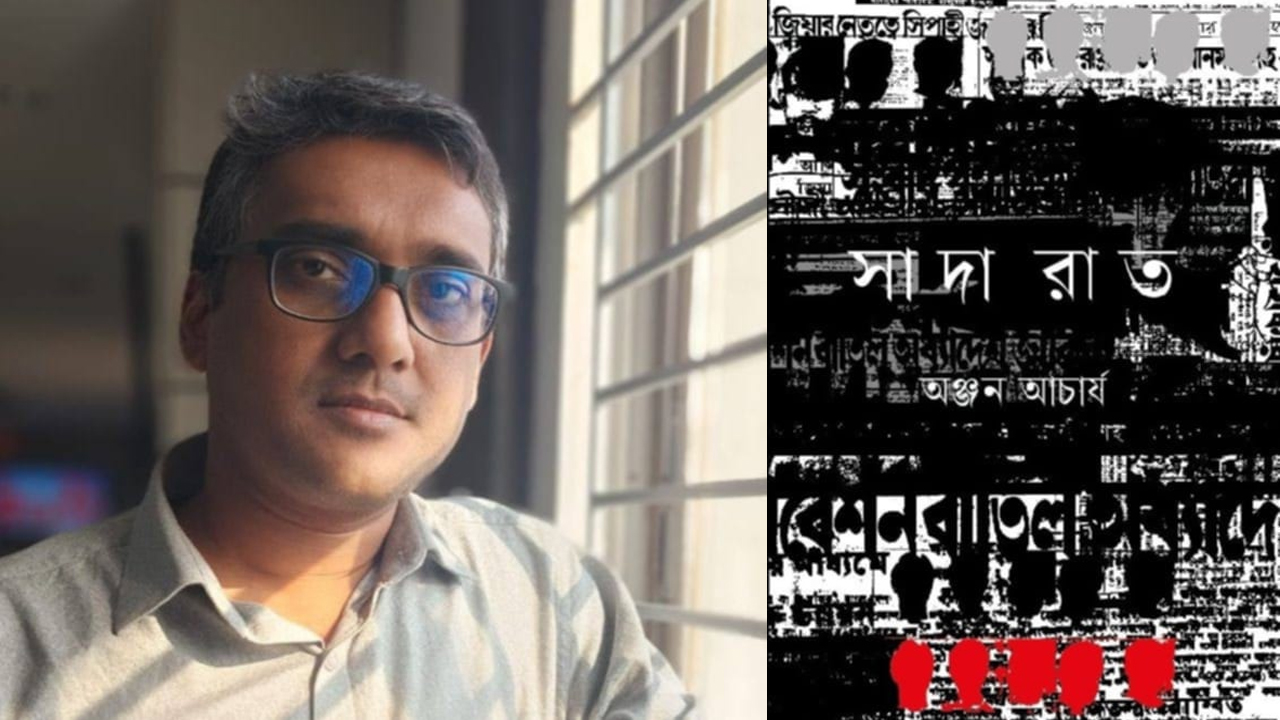রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের চোখে মুসলমান
-
-
|

রবীন্দ্রনাথ যে কালে মধ্যগগণে, সাম্প্রদায়িকতা তখন অন্যতম আলোচিত প্রসঙ্গে পরিণত হয়েছে। সেই বিভাজনের ক্ষত এখনো পুরোটা শুকোয়নি, জের রয়েই গেছে, আমাদের সময় পর্যন্ত এই আালাপ বন্ধ হয়নি। সেই ছেলেবেলা থেকে পাড়াতুতো শুনে আসছি, রবিবাবু সাম্প্রদায়িক। সেই গল্পগুলো যতই হাস্যকর হোক না কেন, সেগুলোর গোপন ও প্রকাশ্য, পলকা ও গভীর সকল রকম প্রভাবের রসায়নের মধ্য দিয়েই আমাদের প্রজন্মের শিশুরাও যে গিয়েছেন, তা খুব ভালো করেই জানি। আমাদের আগের প্রজন্ম যে গিয়েছেন, তাও টের পাই নানান লেখায়, বলায়। পরের যারা আসছেন, জানি না এই সবে তাদের কতদূর কী এসে যাবে, কেননা যুগের বদলে বিতর্কে আগ্রহের বিষয়ও বদলায়। কিন্তু খুবই তো সম্ভাবনা আছে, শুনে শুনেই তাকে লোকে ভালোবাসে কিংবা ঘৃণা করে, ততটা ঘেটেঘুটে দেখবার সময় কই! বরং ভালো হয় না, রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর মুসলমানদের নিয়ে কী ভাবতেন তার একটা চলনসই সংকলন হাতের কাছে থাকলে? অন্তত, লোকে তবে জেনেশুনেই বিষপান করতে পারে। সেই জন্যই এই অসৃজনশীল গ্রন্থনার উদ্যোগ, মুসলমান-প্রসঙ্গগুলোতে রবীন্দ্রনাথের কিছু মতামতের একটা চয়ন, সংকলক কেবল কিছু বাক্য দিয়ে প্রসঙ্গগুলোকে জোড়া দেওয়ার চেষ্টা করেছেন মাত্র, অল্প দুয়েক ক্ষেত্রে নিজস্ব কিছু মত হয়তো এসেছে। তবে এই সংকলন খুবই অসম্পূর্ণ, এই কথা আগেই স্বীকার করে রাখা ভালো। তেমন সম্পূর্ণ একটা সংকলন পেলে মন্দও হতো না।
১.
কোত্থেকে শুরু করা যায়? মুসলমান প্রতিবেশীদের কিংবা মুসলমান শাসকদের রবীন্দ্রনাথ পরদেশী ভাবতেন কিনা, এখান থেকেই তবে যাত্রারম্ভ করি।
‘মুসলমান ছাত্রের বাংলা শিক্ষা’ নামের প্রবন্ধে ঠাকুর মত দিয়েছেন : “ইংরাজি শিক্ষার যেরূপ প্রচলন হইয়াছে, তাহাতে ইংরাজের ইতিহাস, সমাজতত্ত্ব, আচার-বিচার আমাদের কাছে লেশমাত্র অগোচর থাকে না; অথচ তাহারা বহুদূরদেশী এবং মুসলমানরা আমাদের স্বদেশীয়, এবং মুসলমানদের সহিত বহুদিন হইতে আমাদের রীতিনীতি পরিচ্ছদ ভাষা ও শিল্পের আদান-প্রদান চলিয়া আসিয়াছে। অদ্য নূতন ইংরাজি শিক্ষার প্রভাবে আত্মীয়ের মধ্যে প্রতিবেশীর মধ্যে ব্যবধান দাঁড়াইয়া গেলে পরম দুঃখের কারণ হইবে। বাঙালি মুসলমানের সহিত বাঙালি হিন্দুর রক্তের সম্বন্ধ আছে, এ কথা আমরা যেন কখনো না ভুলি।”
স্বীকার করি উদ্ধৃতিটিতে শতভাগ নিঃসংশয় হওয়া গেল না, কিন্তু ইঙ্গিত অন্তত পাওয়া গেল যে, ঠাকুর মুসলমান শাসনকে পরদেশী মনে করতেন না। বাঙালি হিন্দুর সাথে বাঙালি মুসলমানের রক্তের সম্পর্কের ভাবনাটি কিভাবে সম্ভব হয়, আস্ত মুসলমানের শাসনটিই বিদেশি শাসন বলে ভাবা হলে? সন্দেহ আসতে পারে, রবীন্দ্রনাথ হয়তো মনে করতেন, প্রজা মুসলমান এদেশীয়ই ছিল, কিন্তু রাজা মুসলমান বিদেশি!
‘নকলের নাকাল’ প্রবন্ধে পাই সেই সংশয়ের ভঞ্জন : “মুসলমান রাজত্ব ভারতবর্ষেই প্রতিষ্ঠিত ছিল। বাহিরে তাহার মূল ছিল না। এইজন্য মুসলমান ও হিন্দু-সভ্যতা পরস্পর জড়িত হইয়াছিল। পরস্পরের মধ্যে স্বাভাবিক আদানপ্রদানের সহস্র পথ ছিল। এইজন্য মুসলমানের সংস্রবে আমাদের সংগীত সাহিত্য শিল্পকলা বেশভূষা আচারব্যবহার, দুই পক্ষের যোগে নির্মিত হইয়া উঠিতেছিল। উর্দুভাষার ব্যাকরণগত ভিত্তি ভারতবর্ষীয়, তাহার অভিধান বহুলপরিমাণে পারসিক ও আরবি। আধুনিক হিন্দুসংগীতও এইরূপ। অন্য সমস্ত শিল্পকলা হিন্দু ও মুসলমান কারিকরের রুচি ও নৈপুণ্যে রচিত। চাপকান-জাতীয় সাজ যে মুসলমানের অনুকরণ তাহা নহে, তাহা উর্দুভাষার ন্যায় হিন্দুমুসলমানের মিশ্রিত সাজ; তাহা ভিন্ন ভিন্ন দেশে ভিন্ন ভিন্ন আকারে গঠিত হইয়া উঠিয়াছিল।”
এমনকি রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর এতদূর পর্যন্ত মোঘল শাসনকে ভারতীয় শাসন বলে মনে করতেন যে, ১৯১১ সালে দিল্লিতে রাজা জর্জের দরবার আয়োজনের বিরোধিতায় তিনি লিখেছিলেন: “ইতিমধ্যে কার্জন লাটের হুকুমে দিল্লীর দরবারের উদ্যোগ হলো। তখন রাজশাসনের তর্জন স্বীকার করেও আমি তাকে তীব্র ভাষায় আক্রমণ করেছিলুম। সেই প্রবন্ধ যদি হাল আমলের পাঠকেরা পড়ে দেখেন তবে দেখবেন, ইংরেজের সঙ্গে ভারতবাসীর রাষ্ট্রিক সম্বন্ধের বেদনা ও অপমানটা যে কোথায় আমার সেই লেখায় কতকটা প্রকাশ করেছি। আমি এই বলতে চেয়েছিলুম, দরবার জিনিসটা প্রাচ্য, পাশ্চাত্য কর্তৃপক্ষ যখন সেটা ব্যবহার করেন তখন তার যেটা শূন্যের দিক সেইটিকেই জাহির করেন, যেটা পূর্ণের দিক সেটাকে নয়। প্রাচ্য অনুষ্ঠানের প্রাচ্যতা কিসে। সে হচ্ছে দুই পক্ষের মধ্যে আত্মিক সম্বন্ধ স্বীকার করা। তরবারির জোরে প্রতাপের যে সম্বন্ধ সে হলো বিরুদ্ধ সম্বন্ধ, আর প্রভূত দাক্ষিণ্যের দ্বারা যে সম্বন্ধ সেইটেই নিকটের। দরবারে সম্রাট আপন অজস্র ঔদার্য প্রকাশ করবার উপলক্ষ পেতেন, সেদিন তাঁর দ্বার অবারিত, তাঁর দান অপরিমিত। পাশ্চাত্য নকল দরবারে সেই দিকটাতে কঠিন কৃপণতা, সেখানে জনসাধারণের স্থান সংকীর্ণ, পাহারাওয়ালার অস্ত্রেশস্ত্রে রাজপুরুষদের সংশয়বুদ্ধি কণ্টকিত, তার উপরে এই দরবারের ব্যয় বহনের ভার দরবারের অতিথিদেরই ’পরে। কেবলমাত্র নতমস্তকে রাজার প্রতাপকে স্বীকার করবার জন্যেই এই দরবার। উৎসবের সমারোহ দ্বারা পরস্পরের সম্বন্ধের অন্তর্নিহিত অপমানকেই আড়ম্বর করে বাইরে প্রকাশ করা হয়। এই কৃত্রিম হৃদয়হীন আড়ম্বরে প্রাচ্যহৃদয় অভিভূত হতে পারে, এমন কথা চিন্তা করার মধ্যেও অবিমিশ্র ঔদ্ধত্য এবং প্রজার প্রতি অপমান। ভারতবর্ষে ইংরেজের প্রভুত্ব তার আইনে, তার মন্ত্রগৃহে, তার শাসনতন্ত্রে ব্যাপ্তভাবে আছে কিন্তু সেইটেকে উৎসবের আকার দিয়ে উৎকট করে তোলার কোনো প্রয়োজন মাত্রই নেই।” (রবীন্দ্রনাথের রাষ্ট্রনৈতিক মত : প্রবন্ধটি লেখা হয়েছিল শচীন্দ্রনাথ সেনের পলিটিক্যাল ফিলসফি অব রবীন্দ্রনাথ-এর পর্যালোচনা হিসেবে)
দরবার একটা মোঘল প্রথা, সম্রাটের দাক্ষিণ্য সেখানে প্রকাশিত হতো, নৈকট্যের চেষ্টা ছিল তাতে। অন্যদিকে রাজা জর্জের দিল্লী দরবার ছিল কেবল ইংরেজের ক্ষমতার প্রকাশ, এই উপলব্ধিটা প্রকাশের পর খুব সংশয় থাকার কথা না যে, রবিঠাকুর মোঘল শাসনকে বিদেশি হিসেবে দেখতেন না।
শুধু কি তাই? রবীন্দ্রনাথ মোঘল বা পাঠন শাসন তকমার আড়ালে একে ইতিহাসের ধারা থেকে বিচ্ছিন্ন করার বিরুদ্ধেও খানিকটা বলেছেন। ‘ঐতিহাসিক চিত্র’ নামের প্রবন্ধটিতে তিনি যা লিখেছেন সেটা বোধ করি হিন্দু কি মুসলমান নির্বিশেষে যে কোনো আধুনিক ইতিহাসবিদের পূর্বেই ভারতের ইতিহাস সম্পর্কে গভীরতর সত্যোপলব্ধি : “যেমন করিয়াই হউক এখন ভারতবর্ষকে আর পরের চোখে দেখিয়া আমাদের সান্ত্বনা নাই। কারণ, ভারতবর্ষের প্রতি যখন আমাদের প্রীতি জাগ্রত হইয়া উঠে নাই তখন ভারতবর্ষের ইতিহাসকে আমরা বাহির হইতে দেখিতাম; তখন আমরা পাঠান-রাজত্বের ইতিহাস মোঘল-রাজত্বে পাঠ করিতাম। এখন সেই মোঘল-রাজত্ব পাঠান-রাজত্বের মধ্যে ভারতেরই ইতিহাস অনুসরণ করিতে চাহি। ঔদাসীন্য অথবা বিরাগের দ্বারা তাহা কখনো সাধ্য নহে। সেই সমগ্র ধারণা কেবল বিচার ও গবেষণার দ্বারাও হইতে পারে না; কল্পনা এবং সহানুভূতি আবশ্যক।” (ঐতিহাসিক চিত্র, রচনাকাল বাংলা ১৩০৫)
অবশ্য, শাসনটাই ইতিহাসের একমাত্র সত্য নয়, হৃদয়বৃত্তি আর সংস্কৃতি নির্মাণ হয়েছিল কতদূর, সে প্রশ্নও জরুরি। মোঘল-পাঠান শাসনেও মানুষ বেঁচে ছিল, তাদের হৃদয়বৃত্তির যোগও ঘটছিল, তার উপলব্ধিও দুর্লভ নয় রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের মাঝে : “মুসলমান যখন ভারতে রাজত্ব করিতেছিল তখন আমাদের রাষ্ট্রীয় চাঞ্চল্যের ভিতরে একটা আধ্যাত্মিক উদ্বোধনের কাজ চলিতেছিল। সেইজন্য বৌদ্ধযুগের অশোকের মতো মোগল সম্রাট আকবরও কেবল রাষ্ট্রসাম্রাজ্য নয় একটি ধর্মসাম্রাজ্যের কথা চিন্তা করিয়াছিলেন। এইজন্যই সে সময়ে পরে পরে কত হিন্দু সাধু ও মুসলমান সুফির অভ্যূদয় হইয়াছিল যাঁরা হিন্দু ও মুসলমান ধর্মের অন্তরতম মিলনক্ষেত্রে এক মহেশ্বরের পূজা বহন করিয়াছিলেন। এবং এমনি করিয়াই বাহিরের সংসারের দিকে যেখানে অনৈক্য ছিল অন্তরাত্মার দিকে পরম সত্যের আলোকে সেখানে সত্য অধিষ্ঠান আবিষ্কৃত হইতেছিল।” (কালান্তর : সংযোজন)
এতসব সাক্ষ্যের পর বলা যেতেই পারে নিচের পঙ্ক্তিগুলো নিছক পিঠ চাপড়ানোর অভিসন্ধিতে রচিত হয়নি, জাতি সমূহের মিলনের বিচিত্রতাকে ধারণ করার এমন উপলব্ধি খুব বেশি মিলবে না বাংলা সাহিত্যে :
“কেহ নাহি জানে কার আহবানে/ কত মানুষের ধারা/ দুর্বার গ্রোতে এলো কোথা হতে/ সমুদ্রে হলো হারা।/ হেথায় আর্য, হেথা অনার্য/ হেথায় দ্রাবিড়, চীন/ শক-হুন-দল পাঠান মোগল/ এক দেহে হলো লীন।”
২.
এ তো গেল রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর মুসলমানদের বিদেশি বলে মনে করতেন কিনা সেই প্রসঙ্গ। এর আগেকার বাংলা সাহিত্যে মুসলমানদের প্রতি বিদ্বেষ এবং বহুস্থলে তাদের প্রতি অবমাননাকর আচরণ সম্পর্কে কি তিনি সচেতন ছিলেন? কিংবা সে সম্পর্কে উদাসীন ছিলেন? অথবা, বিরূপতার পক্ষাবলম্বী ছিলেন? সাহিত্যে মুসলমানবিদ্বেষ নিয়ে রবীন্দ্রনাথের সচেতনতার উদাহরণ দেখা যাক রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর থেকেই : “সৈয়দ সাহেব বাংলা সাহিত্য হইতে মুসলমান-বিদ্বেষের যে উপকরণ সংগ্রহ করিয়াছেন সেগুলি আমরা অনাবশ্যক ও অসংগত জ্ঞান করি। বঙ্কিমবাবুর মতো লেখকের গ্রন্থে মুসলমান-বিদ্বেষের পরিচয় পাইলে দুঃখিত হইতে হয় কিন্তু সাহিত্য হইতে ব্যক্তিগত সংস্কার সম্পূর্ণ দূর করা অসম্ভব। থ্যাকারের গ্রন্থে ফরাসি-বিদ্বেষ পদে পদে দেখা যায়, কিন্তু ইংরাজি সাহিত্যপ্রিয় ফরাসি পাঠক থ্যাকারের গ্রন্থকে নির্বাসিত করিতে পারেন না। আইরিশদের প্রতি ইংরাজের বিরাগ অনেক ইংরাজ সুলেখকের গ্রন্থে পরিস্ফুট হইয়া উঠে। এ-সমস্ত তর্ক-বিতর্ক ও সমালোচনার বিষয়। বঙ্কিমবাবুর গ্রন্থে যাহা নিন্দার্হ তাহা সমালোচক-কর্তৃক লাঞ্ছিত হউক, কিন্তু নিন্দার বিষয় হইতে কোনো সাহিত্যকে রক্ষা করা অসাধ্য। মুসলমান সুলেখকগণ যখন বঙ্গসাহিত্য রচনায় অধিক পরিমাণে প্রবৃত্ত হইবেন তখন তাঁহারা কেহই যে হিন্দু পাঠকদিগকে কোনোরূপ ক্ষোভ দিবেন না এমন আমরা আশা করিতে পারি না।” (মুসলমান ছাত্রের বাংলা শিক্ষা: খ্যাতনামা জমিদার শ্রীযুক্ত সৈয়দ নবাব আলি চৌধুরী মহাশয় রচিত বাংলা শিক্ষা সম্বন্ধে একটি উর্দু প্রবন্ধের ইরেজি ভাষ্যের রবীন্দ্রনাথকৃত পর্যালোচনা, রচনাকালটা তাৎপর্যপূর্ণ হবার কথা, আলস্যবশতঃ কাজটা করা হয়নি।)
দেখাই যাচ্ছে যে, মুসলমানের প্রতি বঙ্কিমচন্দ্রের বিদ্বেষের বিষয়ে রবীন্দ্রনাথ অত্যন্ত সচেতন, এই আচরণের তিনি পক্ষালম্বীও নন। অবশ্য বর্তমানের পাঠকদের এই দুঃখ থেকে যাবে যে, বঙ্কিমচন্দ্রকে নিয়ে তার মূল্যায়নে এই প্রসঙ্গটি তিনি আনেননি, এলে তা আরো বড় মহত্বের পরিচয় হতো। তার এই মতটি কেবল আমরা জানতে পারছি একজন মুসলমান পাঠকের প্রতিক্রিয়ার বদৌলতেই। কিন্তু সাহিত্য থেকে যেহেতু ব্যক্তিগত সংস্কার সম্পূর্ণ দূর করা সম্ভব না, এবং মুসলমান লেখকদের দিক থেকেও একই ধরনের ক্ষোভের জন্ম হওয়াটা অবাস্তব না, তাই রবীন্দ্রনাথ সাহিত্যকে নিন্দা আর সমালোচনার আলোতেই পাঠ করার পরামর্শ দিয়েছেন।
শুধু সাহিত্যে উপস্থাপনার ত্রুটি নয়, মুসলমান প্রজাদের প্রতি বাস্তব সামাজিক নিপীড়ন নিয়ে তার স্বীকারোক্তিটা স্মরণ করা যাক : “হিন্দু-মুসলমানের সম্বন্ধ লইয়া আমাদের দেশের একটা পাপ আছে; এ পাপ অনেক দিন হইতে চলিয়া আসিতেছে। ইহার যা ফল তাহা না ভোগ করিয়া আমাদের কোনোমতেই নিষ্কৃতি নাই। আর মিথ্যা কথা বলিবার কোনো প্রয়োজন নাই। এবার আমাদিগকে স্বীকার করিতেই হইবে হিন্দু-মুসলমানের মাঝখানে একটা বিরোধ আছে। আমরা যে কেবল স্বতন্ত্র তাহা নয়। আমরা বিরুদ্ধ। আমরা বহুশত বৎসর পাশে পাশে থাকিয়া এক খেতের ফল, এক নদীর জল, এক সূর্যের আলোক ভোগ করিয়া আসিয়াছি; আমরা এক ভাষায় কথা কই, আমরা একই সুখদুঃখে মানুষ; তবু প্রতিবেশীর সঙ্গে প্রতিবেশীর যে সম্বন্ধ মনুষ্যোচিত, যাহা ধর্মবিহিত, তাহা আমাদের মধ্যে হয় নাই। আমাদের মধ্যে সুদীর্ঘকাল ধরিয়া এমন-একটি পাপ আমরা পোষণ করিয়াছি যে, একত্রে মিলিয়াও আমরা বিচ্ছেদকে ঠেকাইতে পারি নাই। এ পাপকে ঈশ্বর কোনোমতেই ক্ষমা করিতে পারেন না। আমরা জানি, বাংলাদেশের অনেক স্থানে এক ফরাশে হিন্দু-মুসলমানে বসে না, ঘরে মুসলমান আসিলে জাজিমের এক অংশ তুলিয়া দেওয়া হয়, হুঁকার জল ফেলিয়া দেওয়া হয়। তর্ক করিবার বেলায় বলিয়া থাকি, কী করা যায়, শাস্ত্র তো মানিতে হইবে। অথচ শাস্ত্রে হিন্দু-মুসলমান সম্বন্ধে পরস্পরকে এমন করিয়া ঘৃণা করিবার তো কোনো বিধান দেখি না। যদি-বা শাস্ত্রের সেই বিধানই হয় তবে সে শাস্ত্র লইয়া স্বদেশ-স্বজাতি-স্বরাজের প্রতিষ্ঠা কোনোদিন হইবে না। মানুষকে ঘৃণা করা যে দেশে ধর্মের নিয়ম, প্রতিবেশীর হাতে জল খাইলে যাহাদের পরকাল নষ্ট হয়, পরকে অপমান করিয়া যাহাদিগকে জাতিরক্ষা করিতে হইবে, পরের হাতে চিরদিন অপমানিত না হইয়া তাহাদের গতি নাই। তাহারা যাহাদিগকে ম্লেচ্ছ বলিয়া অবজ্ঞা করিতেছে সেই ম্লেচ্ছের অবজ্ঞা তাহাদিগকে সহ্য করিতে হইবেই।” (ব্যাধি ও প্রতিকার : আলোচ্য দীর্ঘ প্রবন্ধটির রচনাকাল পাইনি, তবে রচনার শুরুতেই বলা আছে, “কিছুকাল হইতে বাংলাদেশের মনটা বঙ্গবিভাগ উপলক্ষে খুবই একটা নাড়া পাইয়াছে।”)
বঙ্গভঙ্গ বিরোধী রাজনীতিতে মুসলমান সমাজের সংশ্লিষ্টতা বোধ না করাটা যুক্তিহীন ছিল না, বরং তার কার্যকারণ সমাজ বাস্তবতার মাঝেই বিরাজমান ছিল, সেই অবিশ্বাস্যপ্রায় উপলদ্ধিটা এখানে রবীন্দ্রনাথের মাঝে আমরা পাচ্ছি। ওই প্রবন্ধেই রবীন্দ্রনাথ আরো বলছেন : “যাহাদিগকে আমরা ‘চাষা বেটা’ বলিয়া জানি, যাহাদের সুখদুঃখের মূল্য আমাদের কাছে অতি সামান্য, যাহাদের অবস্থা জানিতে হইলে আমাদিগকে গবর্মেন্টের প্রকাশিত তথ্যতালিকা পড়িতে হয়, সুদিনে দুর্দিনে আমরা যাহাদের ছায়া মাড়াই না, আজ হঠাৎ ইংরেজের প্রতি স্পর্ধা প্রকাশ করিবার বেলায় তাহাদের নিকট ভাই-সম্পর্কের পরিচয় দিয়া তাহাদিগকে চড়া দামে জিনিস কিনিতে ও গুর্খার গুঁতা খাইতে আহবান করিলে আমাদের উদ্দেশ্যের প্রতি সন্দেহ জন্মিবার কথা। সন্দেহ জন্মিয়াও ছিল। কোনো বিখ্যাত ‘স্বদেশী’ প্রচারকের নিকট শুনিয়াছি যে, পূবর্বঙ্গে মুসলমান শ্রোতারা তাঁহাদের বক্তৃতা শুনিয়া পরস্পর বলাবলি করিয়াছে যে, বাবুরা বোধ করি বিপদে ঠেকিয়াছে। ইহাতে তাঁহারা বিরক্ত হইয়াছিলেন, কিন্তু চাষা ঠিক বুঝিয়াছিল। বাবুদের স্নেহভাষণের মধ্যে ঠিক সুরটা যে লাগে না তাহা তাহাদের বুঝিতে বিলম্ব হয় নাই। উদ্দেশ্যসাধনের উপলক্ষে প্রেমের সম্বন্ধ পাতাইতে গেলে ক্ষুদ্র ব্যক্তির কাছেও তাহা বিস্বাদ বোধ হয়, সে উদ্দেশ্য খুব বড়ো হইতে পারে, হউক তাহার নাম ‘বয়কট’ বা ‘স্বরাজ’, দেশের উন্নতি বা আর-কিছু। মানুষ বলিয়া শ্রদ্ধাবশত ও স্বদেশী বলিয়া স্নেহবশত আমরা যদি সহজেই দেশের জনসাধারণকে ভালোবাসিতাম, ইংরেজি শিক্ষায় আমাদের পরস্পরের মধ্যে বিচ্ছেদ না ঘটাইয়া মিলনকে যদি দৃঢ় করিতে পারিত, তাহাদের মাঝখানে থাকিয়া তাহাদের আপন হইয়া তাহাদের সর্বপ্রকার হিতসাধনে যদি আমাদের উপেক্ষা বা আলস্য না থাকিত, তবে আজ বিপদ বা ক্ষতির মুখে তাহাদিগকে ডাক পাড়িলে সেটা অসংগত শুনিতে হইত না।”
“হিন্দু-মুসলমান এক হইলে পরস্পরের কত সুবিধা একদিন কোনো সভায় মুসলমান শ্রোতাদিগকে তাহাই বুঝাইয়া বলা হইতেছিল। তখন আমি এই কথাটি না বলিয়া থাকিতে পারি নাই যে, সুবিধার কথাটা এ স্থলে মুখে আনিবার নহে; দুই ভাই এক হইয়া থাকিলে বিষয়কর্ম ভালো চলে, কিন্তু সেইটেই দুই ভাই এক থাকিবার প্রধান হেতু হওয়া উচিত নহে। কারণ, ঘটনাক্রমে সুবিধার গতি পরিবর্তন হওয়াও আশ্চর্যকর নহে। আসল কথা, আমরা এক দেশে এক সুখদুঃখের মধ্যে একত্রে বাস করি, আমরা মানুষ, আমরা যদি এক না হই তবে সে লজ্জা, সে অধর্ম। আমরা উভয়েই এক দেশের সন্তান, আমরা ঈশ্বরকৃত সেই ধর্মের বন্ধনবশত, শুধু সুবিধা নহে, অসুবিধাও একত্রে ভোগ করিতে প্রস্তুত, যদি না হই তবে আমাদের মনুষ্যত্বে ধিক্। আমাদের পরস্পরের মধ্যে, সুবিধার চর্চা নহে, প্রেমের চর্চা, নিঃস্বার্থ সেবার চর্চা যদি করি তবে সুবিধা উপস্থিত হইলে তাহা পুরা প্রহণ করিতে পারিব এবং অসুবিধা উপস্থিত হইলেও তাহাকে বুক দিয়া ঠেকাইতে পারিব।”
৩.
এই প্রশ্নটিকে আবারও তিনি বিচার করেছেন হিন্দু বিশ্ববিদ্যালয় নামের প্রবন্ধটিতে : “কিছুকাল পূর্বে হিন্দু-মুসলমানের মধ্যে এই স্বাতন্ত্র্য অনুভূতি তীব্র ছিল না। আমরা এমন এক রকম করিয়া মিলিয়া ছিলাম যে আমাদের মধ্যেকার ভিন্নতাটা চোখে পড়িত না। কিন্তু স্বাতন্ত্র্য-অনুভূতির অভাবটা একটা অ-ভাবমাত্র, ইহা ভাবাত্মক নহে। অর্থাৎ আমাদের মধ্যে সত্যকার অভেদ ছিল বলিয়াই যে, ভেদ সম্বন্ধে আমরা অচেতন ছিলাম তাহা নহে। আমাদের মধ্যে প্রাণশক্তির অভাব ঘটিয়াছিল বলিয়াই একটা নিশ্চেতনতায় আমাদিগকে অভিভূত করিয়াছিল। একটা দিন আসিল যখন হিন্দু আপন হিন্দুত্ব লইয়া গৌরব করিতে উদ্যত হইল। তখন মুসলমান যদি হিন্দুর গৌরব মানিয়া লইয়া নিজেরা চুপচাপ পড়িয়া থাকিত তবে হিন্দু খুব খুশি হইত সন্দেহ নাই, কিন্তু যে কারণে হিন্দুর হিন্দুত্ব উগ্র হইয়া উঠিল সেই কারণেই মুসলমানের মুসলমানি মাথা তুলিয়া উঠিল। এখন সে মুসলমানরূপেই প্রবল হইতে চায়, হিন্দুর সঙ্গে মিশিয়া গিয়া প্রবল হইতে চায় না। এখন জগৎ জুড়িয়া সমস্যা এ নহে যে, কী করিয়া ভেদ ঘুচাইয়া এক হইব। কিন্তু কী করিয়া ভেদ রক্ষা করিয়াই মিলন হইবে সে কাজটা কঠিন। কারণ, সেখানে কোনো প্রকার ফাঁকি চলে না, সেখানে পরস্পরকে পরস্পরের জায়গা ছাড়িয়া দিতে হয়। সেটা সহজ নহে, কিন্তু, যেটা সহজ সেটা সাধ্য নহে; পরিণামের দিকে চাহিলে দেখা যায় যেটা কঠিন সেটাই সহজ। আজ আমাদের দেশে মুসলমান স্বতন্ত্র থাকিয়া নিজের উন্নতিসাধনের চেষ্টা করিতেছে। তাহা আমাদের পক্ষে যতই অপ্রিয় এবং তাহাতে আপাতত আমাদের যতই অসুবিধা হউক, একদিন পরস্পরের যথার্থ মিলনসাধনের ইহাই প্রকৃত উপায়। ধনী না হইলে দান করা কষ্টকর; মানুষ যখন আপনাকে বড়ো করে তখনই আপনাকে ত্যাগ করিতে পারে। যত দিন তাহার অভাব ও ক্ষুদ্রতা ততদিনই তাহার ঈর্ষা ও বিরোধ। ততদিন যদি সে আর কাহারও সঙ্গে মেলে তবে দায়ে পড়িয়া মেলে। সে মিলন কৃত্রিম মিলন। ছোটো বলিয়া আত্মলোপ করাটা অকল্যাণ, বড়ো হইয়া আত্মবিসর্জন করাটাই শ্রেয়।”
বঙ্গভঙ্গ ও এর বিরোধী আন্দোলনের মধ্য দিয়ে বিভাজনের যে গভীরতাটা টের পাওয়া গেল, তার রূপ স্পষ্টত সাম্প্রদায়িক হলেও নানা ঐতিহাসিক কারণে এই সাম্প্রদায়িকতার সড়কেই উপনিবেশ নিয়ন্ত্রিত ভারতে আধুনিক রাজনীতির বিকাশ ঘটল। হিন্দু ও মুসলমান উভয় সম্প্রদায়ের মাঝে অত্যল্প ব্যতিক্রমীদের একজন রবীন্দ্রনাথ যথাসময়ে এ বিষয়ে সচেতন ও আত্মসমালোচনায় মুখর হয়েছেন। হিন্দু শ্রেষ্ঠত্ব স্বীকারে বাধ্য করে ব্রিটিশবিরোধী যৌথ সংগ্রামে মুসলমানকে যুক্ত করতে যাওয়ার অর্থহীনতা তার কাছে যথাযথরূপেই ধরা পড়েছিল। বঙ্গভঙ্গ বিরোধী আন্দোলন থেকে নিজেকে তিনি গুটিয়েও নেন দ্রুত। পূর্ববঙ্গের মুসলমানদের বিরোধিতার কারণ ও প্রাবল্য তিনি দ্রুতই চিহ্নিত করতে পেয়েছিলেন এবং তাদের ক্ষোভ আর পৃথকতাবোধের যে ন্যায্য কারণ আছে, তাই তুলে ধরলেন। বঙ্গভঙ্গ কিন্তু একটা নির্ধারক প্রশ্ন হয়েছিল পরবর্তী রাজনীতিতে। বঙ্গভঙ্গ-পরবর্তীকালে যখন মুসলমানদের স্বাতন্ত্রের অনুভূতি আর দাবি ক্রমশ চড়াও হতে থাকে, কুলীন জমিদারগোষ্ঠীর স্বার্থের শ্রেষ্ঠত্বকে কেন্দ্রে রেখে বঙ্গভঙ্গবিরোধিতার আন্দোলনে যে ভাববিলাসী এক বাংলার ভাবকল্প গড়ে উঠেছিল, সেটাই কিন্তু উল্টো আচরণ করে ’৪৭ সালে। শরৎচন্দ্র, সুনীতি কুমার চট্টোপাধ্যায়ের মতো নিজেদের ‘হিন্দু সমাজের’ স্বার্থরক্ষকরূপে খুঁজে পাওয়া ব্যক্তিবর্গ ’৪৭ সালে বাংলা ভাগ করার জন্য মরিয়া হয়ে উঠেছিলেন। কারণ মুসলমান ভোটারদের সংখ্যাগরিষ্ঠ যৌথ বাংলায় বাবু সংস্কৃতি, শিক্ষা ও চাকরির একচেটিয়া বাজার হুমকির মুখে পড়েছিল। একই সময়ে কিন্তু শরৎবসু সমেত বাংলা কংগ্রেসেরই আর একটা অংশ হিন্দুস্বার্থের ঊর্ধ্বে বাংলাভাষী সকলের জন্য, সাম্প্রদায়িকতার গণ্ডি ছাড়িয়ে বৃহত্তর একটা কিছুর জন্য লড়াই করেছিলেন। একই কথা বিপরীত দিক দিয়ে মুসলমানদের জন্যও সত্যি। আবুল হাসিমরা প্রবল হয়ে উঠতে পারেননি; যৌথ বাংলার বদলে পাকিস্তান কাম্য হয়ে উঠেছিল নাজিমুদ্দীন, মাওলানা আকরম খান, আবুল মনসুর আহমদ প্রমুখের নেতৃত্বে অধিকাংশের কাছে। মুসলমান ও হিন্দু দুয়ের সাম্প্রদায়িকতা ভরা রাজনৈতিক চেতনার বিকাশে শিক্ষা ও চাকরির প্রশ্নটি গুরুতর ভূমিকা রেখেছিল। পৃথক শিক্ষার সুযোগের বিরোধিতা করেছিল হিন্দু সাম্প্রদায়িকদের একাংশ, বাড়তি সুবিধা দাবি করেছিল মুসলমানের সাম্প্রদায়িক স্বার্থের প্রতিনিধিত্বকারীরা। এর রাজনৈতিক সমাধান হওয়া সম্ভব ছিল, চিত্তরঞ্জন দাশের নেতৃত্বে রাজনীতি কিছুদূর সে পথে অগ্রসরও হয়েছিল। রবীন্দ্রনাথের কী ভূমিকা ছিল সে প্রসঙ্গে?
“আধুনিক কালের শিক্ষার প্রতি সময় থাকিতে মনোযোগ না করায় ভারতবর্ষের মুসলমান হিন্দুর চেয়ে অনেক বিষয়ে পিছাইয়া পড়িয়াছে। সেখানে তাহাকে সমান হইয়া লইতে হইবে। এই বৈষম্যটি দূর করিবার জন্য মুসলমান সকল বিষয়েই হিন্দুর চেয়ে বেশি দাবি করিতে আরম্ভ করিয়াছে। তাহাদের এই দাবিতে আমাদের আন্তরিক সম্মতি থাকাই উচিত। পদ-মান-শিক্ষায় তাহারা হিন্দুর সমান হইয়া উঠে ইহা হিন্দুরই পক্ষে মঙ্গলকর। আমার নিশ্চয় বিশ্বাস, নিজেদের স্বতন্ত্র বিশ্ববিদ্যালয় স্থাপন প্রভৃতি উদ্যোগ লইয়া মুসলমানেরা যে উৎসাহিত হইয়া উঠিয়াছে তাহার মধ্যে প্রতিযোগিতার ভাব যদি কিছু থাকে তবে সেটা স্থায়ী ও সত্য পদার্থ নহে। ইহার মধ্যে সত্য পদার্থ নিজেদের স্বাতন্ত্র্য উপলব্ধি। মুসলমান নিজের প্রকৃতিতেই মহৎ হইয়া উঠিবে এই ইচ্ছাই মুসলমানের সত্য ইচ্ছা।” (হিন্দু বিশ্ববিদ্যালয়)
শিক্ষার ধরনটি যথাযথ এবং বিজ্ঞানমনস্ক থাকলে সম্প্রদায়ের প্রয়োজন মেটাবার জন্য প্রতিষ্ঠিত শিক্ষালয়ও যে শেষ পর্যন্ত সাম্প্রদায়িক ব্যাকরণের ঊর্ধ্বে উঠতে পারে, সেটা নিয়েও তার কার্যকর চিন্তা ছিল।
“এই জন্যই মনে আশঙ্কা হয় যাঁহারা হিন্দু বিশ্ববিদ্যালয় স্থাপন করিতে উদ্যোগী, তাঁহারা কিরূপ হিন্দুত্বের ধারণা লইয়া এই কার্যে প্রবৃত্ত? কিন্তু সেই আশঙ্কামাত্রেই নিরস্ত হওয়াকে আমি শ্রেয়স্কর মনে করি না। কারণ, হিন্দুত্বের ধারণাকে তো আমরা নষ্ট করিতে চাই না, হিন্দুত্বের ধারণাকে আমরা বড়ো করিয়া তুলিতে চাই। তাহাকে চালনা করিতে দিলে আপনি সে বড়ো হইবার দিকে যাইবেই। তাহাকে গর্তের মধ্যে বাঁধিয়া রাখিলেই তাহার ক্ষুদ্রতা ও বিকৃতি অনিবার্য। বিশ্ববিদ্যালয় সেই চালনার ক্ষেত্র। কারণ সেখানে বুদ্ধিরই ক্রিয়া, সেখানে চিত্তকে সচেতন করারই আয়োজন। সেই চেতনার গ্রোত প্রবাহিত হইতে থাকিলে আপনিই তাহা ধীরে ধীরে জড় সংস্কারের সংকীর্ণতাকে ক্ষয় করিয়া আপনাকে প্রশস্ত করিয়া তুলিবেই।”
৪.
প্রবল বিদ্বেষের ওই যুগটাতে কোরবানি দেওয়ার কিংবা গো-রক্ষার আন্দোলন ছিল সাম্প্রদায়িক হিংসার উপলক্ষ। গো-রক্ষার আকুতিকে বহুবার রবীন্দ্রনাথ মস্করা করেছেন, বলেছেন : “গোরু রক্ষার জন্য এই ধর্মান্ধরা মানুষ হত্যায় পিছুপা হয় না।” কিন্তু বাস্তব বুদ্ধিও যথাসম্ভব চালু রেখেছেন, কারণ বাইরের বিদ্বিষ্ট আবহাওয়ায় উভয়পক্ষই যখন অনড়, তখন আপোষের একটা বন্দোবস্ত করাই ধীমানের কাজ। “আমার অধিকাংশ প্রজাই মুসলমান। কোরবানি নিয়ে দেশে যখন একটা উত্তেজনা প্রবল তখন হিন্দু প্রজারা আমাদের এলাকায় সেটা সম্পূর্ণ রহিত করবার জন্য আমার কাছে নালিশ করেছিল। সে নালিশ আমি সংগত বলে মনে করিনি, কিন্তু মুসলমান প্রজাদের ডেকে যখন বলে দিলুম কাজটা যেন এমনভাবে সম্পন্ন করা হয় যাতে হিন্দুদের মনে অকারণে আঘাত না লাগে, তারা তখনই তা মেনে নিল। আমাদের সেখানে এ পর্যন্ত কোনো উপদ্রব ঘটে নি। আমার বিশ্বাস তার প্রধান কারণ, আমার সঙ্গে আমার মুসলমান প্রজার সম্বন্ধ সহজ ও বাধাহীন।”
৫.
শিবাজি বন্দনা প্রসঙ্গেও কিছু কথা বলা আবশ্যক। রবীন্দ্রনাথের রাজনীতির চিন্তার বিকাশের ধারাটি আমরা বঙ্গভঙ্গ বিষয়ক আমাদের আলোচনায় ইতোমধ্যেই খেয়াল করেছি। তিনি নিজেই লিখেছেন তখন তিনি হিন্দু-মুসলমানের প্রতিবেশিত্বের সংকট বিষয়ে সচেতন ছিলেন না অন্যদের মতোই। ১৯০২ সালে লেখা ‘শিবাজি উৎসব’ কবিতা দিয়ে তাই তাকে চেনা যাবে না পুরোপুরি। অন্যদিকে এটাও স্মরণ রাখা দরকার, শিবাজিকে শুধু মুসলমান মোঘলের বিরুদ্ধে হিন্দু বিদ্রোহী হিসেবে দেখাটাও চরম সাম্প্রদায়িক কাজ হবে। কেন্দ্রীভূত এবং মোঘল সাম্রাজ্যের বিরুদ্ধে আঞ্চলিক বহু বিদ্রোহই তো ঘটেছে। এইখানে সাম্প্রদায়িকতার বাইরেও আর একটা হিসেব নেওয়া দরকার, শিবাজি মারাঠা জনগোষ্ঠীর ঐক্য-সংহতি এবং জাতীয়তাবাদের প্রতীক। সেটা ধর্মীয় চেহারা পেয়েছে, তার জন্য সময় অনেকখানি দায়ী; বেশ খানিকটা দায়ী আওরঙ্গজেবের ধর্মীয় আক্রমণ, এবং প্রায় বিনা উস্কানিতে নতুন নতুন রাজ্য দখল করে দাক্ষিণাত্যকে অস্থিতিশীল করার নীতি। এই আগ্রাসী নীতির কাছে বিজাপুর ও গোলকুণ্ডা নামের দুটি প্রতাপশালী মুসলিম রাজ্য প্রতিরোধ গড়ে তুলতে ব্যর্থ হলেও শিবাজী সফল হন। বর্গীর হামলা বাংলাদেশের হিন্দু-মুসলমান উভয়ের জন্যই বিপর্যয়কর হয়েছিল। লুণ্ঠন বিষয়ে আমাদের আজকের ধারণা ও নীতি দিয়ে মধ্যযুগকে পাঠ করা সুবিবেচনাপ্রসূত হবে না। তুলনীয়, ফরায়েজি আন্দোলন বাংলা এলাকার মুসলমান কৃষকের জমিদারবিরোধী চেতনার একটা প্রকাশ, এটা সাম্প্রদায়িক চেহারা পেয়েছে কতগুলো বাস্তব ঐতিহাসিক কারণেই। রবীন্দ্রনাথ শিবাজী-পরবর্তী শাসকদের সম্পর্কে তার মূল্যায়নটি জানাচ্ছেন : “শিবাজি একসময় ধর্মরাজ্যস্থাপনের ভিত গেড়েছিলেন। তাঁর যে অসাধারণ শক্তি ছিল তদ্দ্বারা তিনি মারাঠাদের একত্র করতে পেরেছিলেন। সেই সম্মিলিত শক্তি ভারতবর্ষকে উপদ্রুত করে তুলেছিল। অশ্বের সঙ্গে অশ্বারোহীর যখন সামঞ্জস্য হয় কিছুতেই সে অশ্ব থেকে পড়ে না; শিবাজির হয়ে সেদিন যারা লড়েছিল তাদের সঙ্গে শিবাজির তেমনি সামঞ্জস্য হয়েছিল। পরে আর সে সামঞ্জস্য রইল না, পেশোয়ারদের মনে ও আচরণে ভেদবুদ্ধি, খণ্ড খণ্ড স্বার্থবুদ্ধি তীক্ষ্ণ হয়ে ক্ষণকালীন রাষ্ট্রবন্ধনকে টুকরো টুকরো করে দিলে।”
মহারাষ্ট্রের বিবেচনায় শিবাজী যতটুকু জাতীয়তাবাদী চেতনার উন্মেষের প্রতীক, বাংলার জন্য তা বর্গীর হামলার স্মৃতি। আমাদের দেশেই প্রচলিত বহু জনপ্রিয় ইতিহাস বইতে সুলতান মাহমুদের চরিত্রচিত্রণেও এই জটিলতাটা ধরা পড়ে। দুইজনের মাঝে মিলটাও অদ্ভুত। সুলতান মাহমুদ মধ্য এশিয়ায় তার সাম্রাজ্য বিস্তারের লড়াইয়ের রসদ জোগাড় করতেন নিয়মিত বিরতিতে উত্তর ভারতের সোমনাথ সমেত কতগুলো মন্দির ও নগর লুণ্ঠন করে। কাছাকাছি কাজই বর্গীরা করত মোঘলদের বিরুদ্ধে তাদের রাষ্ট্রনির্মাণের সংগ্রামে বাংলার মতো দুর্বল প্রদেশগুলো থেকে ‘চৌথ’ আদায় করে।
যদুনাথ সরকারের আওরঙ্গজেবের জীবনী পাঠ করলেও যে কেউ দেখবেন, তিনি শিবাজির প্রশংসা করেছেন কেবল এইটুকু যে, তিনি ধর্মীয় চেতনায় মগ্ন ছিলেন, স্বাধীন হিন্দু মারাঠা সাম্রাজ্যের স্বপ্ন দেখেছেন, নারী ও সাধু প্রকৃতির ব্যক্তিদের ওপর কখনো নির্যাতন চালাননি, সামরিক যোগ্যতা তার অসাধারণ ছিল। কিন্তু পরবর্তীকালে তার উত্তরাধিকারীরা কতটা দুর্বত্ত প্রকৃতির ছিল, সেটা উল্লেখ করতে কখনোই ভোলেননি তিনি। আওরঙ্গজেবের চরিত্রচিত্রণেও সাধ্যমতো নিরপেক্ষ থাকার চেষ্টাই যদুনাথ সরকারের মতো তুলনামূলকভাবে সাম্প্রদায়িকতা-আচ্ছন্ন-কালের ইতিহাসবিদ করেছেন, তার অসাধারণ সব কৃতিত্ব, প্রজ্ঞা আর কর্মদক্ষতার প্রশংসা করেছেন। আওরঙ্গজেবকে মহৎহৃদয় হিসেবে চিত্রিত করাটা সর্বস্থলে সম্ভব হয়নি, সেটার জন্য আওরঙ্গজেব নিজেই অনেকখানি দায়ী। শিবাজির নারী, শিশু ও ধর্মীয় ব্যক্তিদের ওপর আক্রমণ না করার নীতির প্রশংসা কোনো কোনো মুসলমান ইতিহাসবিদও করেছেন। কিন্তু গুরুতর আর একটি প্রসঙ্গ না এসে পারে না বর্গীদের উল্লেখের প্রশ্নেই। ভারতে জাতীয়তার প্রশ্নগুলো প্রায়ই সরল থাকে না। যে হিসেবে বর্গীরা বহিরাগত এবং লুণ্ঠনজীবী, সেই হিসেবেই কিন্তু প্রশ্ন করা যেতে পারে, দিল্লির মোঘল কিংবা তার আগেকার সুলতানরাও বাংলার জন্য তাই ছিলেন না কেন। অজস্র পর্যটকের বর্ণনায় দারিদ্র্যপীড়িত বাংলার যে কৃষক আর কারিগরের উল্লেখ পাওয়া যায়, যারা ছিলেন দিল্লিশ্বরদের বৈভবের প্রধান উৎস, তাদের সেই চিরস্থায়ী দারিদ্র্যের কি প্রধান কারণ নয় এই পরাধীনতা? মারাঠারা এই কেন্দ্রীয় শাসনের বিরুদ্ধে আঞ্চলিক আকাঙ্ক্ষার একটা বহিঃপ্রকাশ ছিল, এমন বহিঃপ্রকাশ বাংলাতেও অজস্রবার ঘটেছে।
৬.
উপনিবেশ-পূর্ববর্তী শাসন নিয়ে ব্রিটিশদের ঐতিহাসিক মিথ্যাচারকে খণ্ডনের যে প্রক্রিয়া ঊনিশ শতকেই শুরু হয়েছিল, রবীন্দ্রনাথ তার উৎসাহী সমর্থক ছিলেন। অক্ষয়কুমার মৈত্রেয় রচিত সিরাজদ্দৌলা প্রসঙ্গে তাঁর লেখাটাতে এর একটা ছাপ ভালোভাবেই আছে : “এমন সময়ে সিরাজদ্দৌলা যৌবরাজ্য গ্রহণ করিলেন এবং ইংরাজের স্বেচ্ছাচারিতা দমন করিবার জন্য কঠিন শাসন বিস্তার করিলেন। রাজমর্যাদাভিমানী নবাবের সহিত ধনলোলুপ বিদেশী বণিকের দ্বন্দ্ব বাঁধিয়া উঠিল। এই দ্বন্দ্বে বণিক-পক্ষে গৌরবের বিষয় কিছুই নাই। সিরাজদ্দৌলা যদিচ উন্নতচরিত্র মহৎ ব্যক্তি ছিলেন না, তথাপি এই দ্বন্দ্বের হীনতা-মিথ্যাচার প্রতারণার উপরে তাঁহার সাহস ও সরলতা, বীর্য ও ক্ষমা রাজোচিত মহত্বে উজ্জ্বল হইয়া ফুটিয়াছে। তাই ম্যালিসন তাঁহার উল্লেখ করিয়া বলিয়াছেন, ‘সেই পরিণাম দারুণ মহানাটকের প্রধান অভিনেতাদের মধ্যে সিরাজদ্দৌলাই একমাত্র লোক যিনি প্রতারণা করিবার চেষ্টা করেন নাই।” (সিরাজদ্দৌলা : শ্রী অক্ষয়কুমার মৈত্রেয়-প্রণীত; রচনাকাল ১৩০৫)
‘মুসলমান ছাত্রের বাংলা শিক্ষা’ প্রবন্ধের কথা আরেকবার উল্লেখ করা যাক, যেখানে শিক্ষাব্যবস্থায় ইতিহাসের পাঠকে ঔপনিবেশিকদের লেপে দেওয়া মিথ্যাচার থেকে মুক্ত করার বিষয়ে সচেনতার প্রমাণ দিতে রবীন্দ্রনাথ অক্ষয় মৈত্রেয়’র প্রবন্ধটির উল্লেখ করেছিলেন : “সম্প্রদায়গত পক্ষপাতের হাত একেবারে এড়ানো কঠিন। ইউরোপীয় ইতিহাসের অনেক ঘটনা ও অনেক চরিত্রচিত্র প্রটেস্টান্ট লেখকের হাতে একভাবে এবং রোমান ক্যাথলিক লেখকের হাতে তাহার বিপরীতভাবে বর্ণিত হইয়া থাকে। ইউরোপে দুই ধর্মসম্প্রদায়ের বিদ্যালয় অনেক স্থলে স্বতন্ত্র, সুতরাং ছাত্রদিগকে স্ব সম্প্রদায়ের বিরুদ্ধ কথা শিক্ষা করিতে বাধ্য হইতে হয় না। কিন্তু ইংরাজ লেখকের সকল প্রকার ব্যক্তিগত ও জাতিগত সংস্কার আমরা শিরোধার্য করিয়া লইতে বাধ্য, এবং সেই-সকল সংস্কারের বিরুদ্ধে কোনো বাংলা বই রচিত হইলে তাহা কোনো বিদ্যালয়ে প্রচলিত হইবার কোনো সম্ভাবনা থাকে না। ইংরাজ লেখকেরই মত বাংলা বিদ্যালয়ের আদর্শ মত, সেই মত অনুসারে পরীক্ষা দিতে হইবে, নতুবা পরীক্ষার নম্বরেই দেখা যাইবে সমস্ত শিক্ষা ব্যর্থ হইয়াছে। অনেক আধুনিক বাঙালি ঐতিহাসিক মুসলমান রাজত্বের ইতিহাসকে ইংরাজ-তুলিকার কালিমা হইতে মুক্ত করিবার জন্য চেষ্টা করিতেছেন। অক্ষয়বাবু তাঁহার সিরাজচরিতে অন্ধকূপহত্যাকে প্রায় অপ্রমাণ করিতে কৃতকার্য হইয়াছেন। কিন্তু প্রমাণ যতই অমূলক বা তুচ্ছ হউক পরীক্ষাতিতীর্ষু বালক মাত্রই অন্ধকূপহত্যা ব্যাপারকে অসন্দিগ্ধ সত্য বলিয়া স্বীকার করিতে বাধ্য।”
এ বিষয়ে রবীন্দ্রনাথ আরো বলছেন : “অতএব বক্তামহাশয়ের বিবেচনা করিয়া দেখা কর্তব্য, পাঠ্যপুস্তকের মতামত সম্বন্ধে আমরা কঠিন শৃঙ্খলে আবদ্ধ। যতদিন না স্বাধীন-গবেষণা ও সুযুক্তিপূর্ণ বিচারের দ্বারা আমরা ইংরাজ সাহিত্যসমাজে প্রচলিত ঐতিহাসিক কুসংস্কারগুলিকে বিপর্যস্ত করিয়া দিতে পারি ততদিন আমাদের নালিশ গ্রাহ্য হইবে না। আমরা হিন্দু ও মুসলমান লেখকগণকে ইতিহাস-সংস্কারব্রত গ্রহণ করিতে আহবান করি। শ্রীযুক্ত কালীপ্রসন্ন বন্দ্যোপাধ্যায়ের ন্যায় দুই-একজন হিন্দু লেখক এই দুরূহ সাধনায় রত আছেন, কিন্তু ইতিহাসের উপকরণমালা প্রায়ই পার্সি উর্দুভাষায় আবদ্ধ, অতএব মুসলমান লেখকগণের সহায়তা নিতান্তই প্রয়োজনীয়।”
৭.
হিন্দু আর মুসলমানের পৃথকতা বিষয়ে সম্পূর্ণ সচেতন ছিলেন রবীন্দ্রনাথ। বিশ শতকের প্রথমার্ধটি ছিল এই দুই সম্প্রদায়ের মুখোমুখি রাজনীতির ইতিহাস। উগ্রগন্ধী সাম্প্রদায়িক রাজনীতির সেই যুগে খুব কম মানুষই ভবিষ্যতের মিলনে আশা রেখেছিলেন, কেউ কেউ অমিলটাকে ধামাচাপা দিয়ে রাজনৈতিক জোড়াতালির সুবিধার পক্ষে ছিলেন। রবীন্দ্রনাথ মুসলমানের সাংস্কৃতিক স্বাতন্ত্র্যের আকাঙ্ক্ষাকে সর্বদা মূল্য দিয়েছেন, কিন্তু মিলন তার কাছে অসম্ভব কল্পনা ছিল না। তার পথও তিনি দেখেছেন : “কিন্তু বিশেষ শাস্ত্রমতের অনুশাসনে বিশেষ করিয়া যদি কেবল বিশেষ পশুহত্যা না করাকেই ধর্ম বলা যায় এবং সেইটে জোর করিয়া যদি অন্য ধর্মমতের মানুষকেও মানাইতে চেষ্টা করা হয়, তবে মানুষের সঙ্গে মানুষের বিরোধ কোনোকালেই মিটিতে পারে না। নিজে ধর্মের নামে পশুহত্যা করিব অথচ অন্যে ধর্মের নামে পশুহত্যা করিলেই নরহত্যার আয়োজন করিতে থাকিব, ইহাকে অত্যাচার ছাড়া আর-কোনো নাম দেওয়া যায় না। আমাদের আশা এই যে, চিরদিন আমাদের ধর্ম আচারপ্রধান হইয়া থাকিবে না। আরো-একটি আশা আছে, একদিন হিন্দু ও মুসলমানের মধ্যে দেশহিতসাধনের একই রাষ্ট্রীয় আইডিয়াল যদি আমাদের রাষ্ট্রতন্ত্রে বাস্তব হইয়া উঠে তবে সেই অন্তরের যোগে বাহিরের সমস্ত পার্থক্য তুচ্ছ হইয়া যাইবে।” (ছোটো ও বড়; ১৩২৪ সাল)
৮.
বলাই বাহুল্য, রবীন্দ্রপাঠ সম্পূর্ণ হয়ে ওঠেনি, অন্য অনেকেরই মতো। সেটুকু পড়ার মাঝে রবীন্দ্রনাথের দিক থেকে বলার মতো তেমন কোনো সাম্প্রদায়িক উক্তি বা মত বর্তমান সংকলক পাননি। যে যা খোঁজে তাই নাকি সে কেবল দেখতে পায়! হতেই পারে সেকারণেই অন্যরূপ দৃষ্টান্তগুলো চোখ এড়িয়ে গেছে। হয়তো উদ্ধৃত ধারণাগুলোর বাইরে আরো বহু প্রকার মত রবীন্দ্রনাথের ছিল, যা আমাদের অগোচরে তিনি লিখে রেখেছেন। তেমন কিছুর সন্ধানের আশাতেও যদি ঠাকুরের বেটার সাথে ভবিষ্যতে আরো কিছু মোলাকাত হয়, মন্দ হবে না তা।